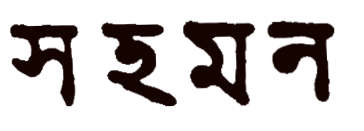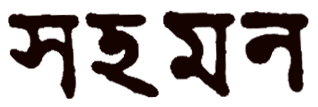ঠাকুমার কাছে আমাদের গ্রামে মহামারির কথা শুনেছিলাম। ১৩৫০ সালে বাংলায় ধানের ফলন কম হয়েছিল। তখন সব জমিই এক ফসলি। বছরে একবার চাষ থেকেই সারা বছরের খাওয়া-পরার সংস্থান করতে হত। যুদ্ধের অজুহাতে সরকার কিন্তু সেবছরও খাজনা ষোলো আনাই উশুল করে নিল । যাদের জমিজমা বেশি, খাজনা পুরো মিটিয়ে খোরাকির অতিরিক্ত কিছু সঞ্চয় থাকল বটে। নিতান্ত গরিব চাষী সবাই, এমনকি অনেকেই কাছারিতে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে আংশিক খাজনা মিটিয়েও, আতান্তরে পড়ল। ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের অবস্থা আরও করুণ। যেটুকু খোরাকি ছিল তাতে বেশিদিন চলবার নয়। অচিরেই অন্ন সংস্থানে টান পড়ল। যাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার সামর্থ্য ছিল, অগ্নিমূল্যের বাজারে তাদেরই কার্পণ্য করে চলতে হচ্ছে, তখন গরিবদের বড় অসহায় অবস্থা। দুর্ভিক্ষ শুরু হ’ল। আমাদের গ্রামেই জমিদারের বাস ছিল। ক্ষেতমজুররা জমিদারের কাছে হাত পাতল। জমিদার তখন নিজেই শঙ্কিত, বকেয়া খাজনার দায়ে বুঝি জমিদারি নিলামে ওঠে। জমিদারের যা কিছু সঞ্চয় ছিল ধনে-বলে জমিদারি ঠাঁট বজায় রাখার জন্য রক্ষিত। ফলে তারা মুখের অন্ন পেল যৎসামান্য, সরকারি ত্রাণের সান্ত্বনা পেল বেশি।
দুর্ভিক্ষ একা আসে না। অচিরেই শুরু হ’ল কলেরার মহামারি। ডাক্তার-বদ্যি তখন ভয়ে গ্রামে আসছে না। দুরদুর করে মানুষ মরছে। অঞ্চলে এই গ্রামেই কলেরার প্রাদুর্ভাব বেশি হয়েছিল। খিদের জ্বালায় আর মড়কের বিভীষিকায় অসহায় মানুষ তখন দেবদেবীর থানে হত্যে দেয়, পীরের দরগায় মানত করে, নিজেদের ভাগ্যের ওপর দোষারোপ করে ভাগ্যের মদত চায়। হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই। নিজ নিজ সমাজে যত ধর্মীয় লোকাচার সব পালন করে। আর অবসন্ন দেহে লাশ বহন করে। দু’মাসের মধ্যে মানুষের লাশে গ্রাম উজাড় হয়ে গেল। গুটিকয় পরিবার বাদে আর সব পরিবারে একাধিক পরিজন হারানোর হাহাকার।
তখন অপর্যাপ্ত সরকারি ত্রাণ পৌঁছলে দু’বেলা আধপেটা খেয়ে ধ্বস্ত দেহে, মন জুড়ে অন্ধকারের বিষাদ নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকা। দুর্বোধ্য সে অন্ধকার। হিন্দু মনে অপদেবতার মহিমা অপরিসীম। মুসলমান মনে গজবের কথা-কাহিনী খেলে বেড়ায়। সন্ধ্যা রাতেই নিশুতি রাতের মায়ায় তারা অনুভব করে, আনাচে-কানাচে অশরীরীর ছায়া ঘুরে বেড়ায়। গুমরানো কান্না শুনতে পায়। তাদের মনে হয়, এ বুঝি সমাসন্ন বিপদের পদচারণা। জন্মভূমি মনে হয় বধ্যভূমি। গরিব পরিবারগুলোর গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। কেবল ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের বাস ছিল মুচিপাড়ায়। পাড়া পুরো খালি হয়ে গিয়েছিল। যাদের জমিজমা ছিল, তারা থেকে গেল জীবিকার বাধ্যবাধকতায়। তারা ‘গ্রাম বন্ধক’এর নানা তুকতাক করে মনকে বোঝাল।
আমাদের গ্রামের নাম রানীহাটি। জমিদারি অধিগ্রহণের সময় পর্যন্ত তিন শতাধিক গ্রাম ছিল রানীহাটি পরগণার অধীন। এটি ছিল জমিদারির বড় তালুক। জমিদারির মালকিন অন্যত্র বাস করতেন। তবে দু’-তিন মাসে অন্তত একবার আসতেন এখানে। দু’-এক সপ্তাহ কাটাতেন। তাঁর থাকার জন্য কাছারিবাড়ি লাগোয়া ছোট রাজবাড়ি ছিল। তাঁকে সকলে রানি বলত। সেই মতো গ্রামের নাম রানিহাটি। নি:সন্তান রানী বৃদ্ধাবস্থায় এখানকার জমিদারি বিক্রি করে দিয়ে আমাদের গ্রাম থেকে চিরবিদায় নেন। জমিদারির একটা ছোট অংশ কিনে নেন এই গ্রামের এক সম্পন্ন কৃষক। সময়টা গত শতকের শুরুর দিকে। বর্তমানে রানির স্মারকচিহ্ন বলতে টিকে আছে গ্রামের নাম আর গ্রামের মাঠে মজে যাওয়া রানিপুকুরের ভাঙা ঘাট।
গ্রামটি শিক্ষা-দীক্ষায় আজও পশ্চাৎপদ। পুরনো অন্ধ বিশ্বাস কিছু বিদায় নিলেও নবীকৃত অন্ধ বিশ্বাস জাঁকিয়ে বসেছে। অধিকাংশের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ নেই। যে ক’জন উচ্চশিক্ষা নিয়েছে, তারাও গ্রামের সংস্কার-সংস্কৃতিতেই বিশ্বাসী। আশপাশের বিশ-পঁচিশটা গ্রাম ধরলে সবচেয়ে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক এই গ্রামের। গ্রামটি মুসলমান প্রধান। সংখ্যালঘু হিসেবে সরকারি অবহেলা-বঞ্চনার কথা আসতে পারে। কিন্তু গ্রামটির পশ্চাদ্ভূমি বাদ দিয়ে ভাবা ঠিক হবে না। পশ্চাদ্ভূমির ইতিবৃত্তের বাস্তবতায় গ্রামটির বর্ধিষ্ণু চেহারা নেওয়া উচিত ছিল।
আমাদের গ্রামের আমার বয়সী সকলে ছেলেবেলায় এগ্রামে পঞ্চাশের মহামারির কাহিনী শুনেছি বড়দের মুখে। এখনও সময়ে সেসব প্রসঙ্গ চলে আসে। আজ করোনার আবহে ভাবি, সেদিনের ক্ষত বোধহয় আজও এগ্রামের মানুষের মনের কোণে লুকিয়ে আছে। সেদিন মানুষের মনে গেড়ে বসা অসহায়তা-বোধ, অন্ধ বিশ্বাস বুঝি আজও মানুষের অবচেতনে দাগ কাটে।
বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে ভারত বর্তমানে ভালই এগিয়েছে। উন্নত চিকিৎসা-পদ্ধতি হাতে আছে। তার একটা প্রভাব মানুষের মধ্যে থেকেই যায়। কিন্তু দেশের শাসক শিবির ও ধর্মীয় জগতের গুরুস্থানীয় অনেকের পাকা মাথা করোনা নিয়ে কুসংস্কার ও অপবিজ্ঞানের ফেরি শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে দেশে বর্তমান জনস্বাস্থ্যের অব্যবস্থায় আমাদের গ্রামের কথা ভেবে মনে আশঙ্কা একটা জাগে বৈকি।