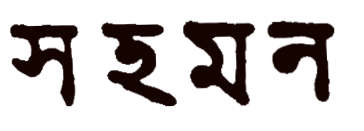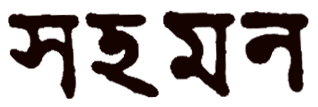পুজোর মরশুম শেষ হয়ে গেছে, তবুও রেশ যেন থেকেই গেছে। যেমন পুজো আসার অনেক আগে থেকেই আগমনীর মেজাজ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। সেই আগমনীর সময়েই এবার পুজোর বাজারে এসেছিল একটি গান। বকুলতলার মেলা আর ঘোষবাবুদের খোঁচা দেওয়ার পর তাঁরা হাজির করেছিলেন ছৌ নাচ আর পুজোর মিশেল। এক fusion inclusiveness যাকে বলা যায়। শহর কলকাতার বাইরের আবেগ, ভদ্রবিত্তসমাজের বাইরের সংস্কৃতি উদযাপিত হচ্ছে, এটা স্বাভাবিকভাবেই ভালোলাগার কথা। তবে আরও কিছু কথা, সাথে কিছু প্রশ্ন সাথে করে এসেই যাচ্ছে।
ছৌ নাচ নিয়ে একটু পড়াশোনা করলে দেখা যায়, সরাইকেল্লা ও পুরুলিয়া ছৌ-তে মুখোশ ব্যবহৃত হলেও, ময়ূরভঞ্জ ছৌ-তে হয় না। অর্থাৎ তুলনায় উত্তরের জেলাগুলোতে মুখোশের ব্যবহার আছে। এখনকার সাংস্কৃতিক ভূগোল জানতে গেলে ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাওয়া ভূগোলটাকে চিনতে হবে। এই প্রসঙ্গে 'ছত্রাক' পত্রিকার নবম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় রাজেশ্বর মিত্র উল্লেখ করেছেন, "সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে মুখোশনৃত্য লাসায় কেবলমাত্র লাসা সম্প্রদায় দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাঁকে বলা হয় ছাম। এই ছাম শব্দটি ক্রমে ছাউ, ছৌ বা ছো তে পরিণত হওয়া আমাদের দেশে আশ্চর্য নয়। ছো শব্দটি তিব্বতীয় এবং একে অবলম্বন করে বহু প্রকার বীর রসাত্মক নৃত্য আছে- এটাও যথার্থ। অতএব ছো বা ছাম নৃত্যাদি থেকে বর্তমান ছৌ বা ছো যে আমাদের দেশে আসতে পারে এমন অনুমান নেহাত কল্পনা বলে মনে হয় না; বিশেষত আমাদের সাধক ও তিব্বতের সাধকদের মধ্যে যখন একদা যাওয়া আসা বা Culture-এর আদান-প্রদান ছিল।"
এখানে বোঝা দরকার সেসময় তিব্বত এখনকার চীন-অধিকৃত তিব্বতের মতো এতদুরের ছিল না। কার্জনের লাসা অভিযানের আগে বর্তমান অরুণাচল ব্রিটিশ ভারতের নয়, তিব্বত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। তেমনই ইঙ্গ-ভূটানী যুদ্ধের আগে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স এলাকা ভূটানের অংশ ছিল। সেকারণে তিব্বতীয় সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব এইসব অঞ্চলে পড়েছে, এখনও রয়েছে। চাইলে ভূটানের জাতীয় সঙ্গীত শুনে নিতে পারেন। ভূটানের দক্ষিণে মানে এখনকার ডুয়ার্স, আসাম ছাড়িয়ে উত্তর ও মধ্যবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই প্রভাব ছড়িয়ে ছিল। এখনও 'নকশাল' থেকে 'মোমো', অনেক তিব্বতি শব্দ আমাদের শব্দভাণ্ডারে ঢুকেছে। এছাড়াও পুরাণে বর্তমান হিন্দুধর্মের অনেক দেবদেবীর জন্মস্থান হিসেবে পর্বত দেখানো হয়েছে। অদ্রিজা, গিরিজা, পার্বতী এইসব নামের মধ্যে তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চল ধরা পড়ে। তিব্বতের লাল জম্ভল ও হর-পার্বতীপুত্র গণেশের মূর্তির সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। আর শিবের পৌরাণিক আবাস কৈলাস পর্বত, যা তিব্বতে। গৌড়পতি শশাঙ্কও শৈব ছিলেন। উত্তরবঙ্গে তিব্বতি প্রভাব নকশালবাড়ি, তোর্সা প্রভৃতি শব্দ থেকেই পরিস্কার হয়ে যায়। এমনকি শ্মশানচারী শিব বা কালীর দিকবিদিকশূন্য দৃশ্যকল্পও সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বাংলা'র নয়, তিব্বতের এবং ডুয়ার্সের কাছের ভাবর অঞ্চলের। চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে সারা বৈশাখ মাস ও জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো তারিখে অনুষ্ঠিত রহিন উৎসব পর্যন্ত ছৌ নাচ নাচা হয়ে থাকে। পুরুলিয়া জেলায় শিবের গাজন উপলক্ষে ছৌ নাচের আসর বসে।
আরও একটা বিষয় বোঝার আছে। গৌড় সালতানাত আর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবীর সীমা এক ছিল না। কোচবিহারের কামরূপ রাজ্য মুর্শিদাবাদের নবাবের আওতার বাইরেই ছিল। সেজন্য পলাশী-বক্সারের যুদ্ধে নবাবের পতন হলেও ত্রিপুরার মতো কোচবিহারও দেশীয় রাজ্য হিসেবে থাকতে পেরেছে। একসময় বাংলার প্রতিবেশী তিব্বতের সাথে ধরলা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতির মাধ্যমে আরবদের ব্যবসা চলতো। ইসলামের উত্থানের আগেও এই বাণিজ্য ছিল, তারও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেই বাণিজ্যেরই স্বাক্ষী লালমনিরহাটের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। এমনকি বক্তিয়ার খলজিও এই পথ ধরে তিব্বত আক্রমণে গিয়ে সিকিম-ভূটান সীমান্তের চুঙ্গি বা চুম্বি উপত্যকায় আহত হয়ে পরে প্রাণ হারিয়ে ছিলেন। সেই অভিযানে বক্তিয়ারকে পথ দেখিয়েছিলেন আলি মেচ নামে মেচজাতির জনৈক সর্দার। এই অঞ্চলে এখনও মেচ, কোচ ইত্যাদি জাতির পাশাপাশি অন্যান্য আদিবাসীরাও রয়েছেন। এমনকি অসুর সম্প্রদায়েরও পাঁচশ পরিবার জলপাইগুড়ির ভূটান সংলগ্ন নাগরাকাটার কেরণ চা বাগানে রয়েছেন বলে জানা যায়।
তাহলে কি মানে করা যায় মূলত তিব্বতি দেবতা শিবের জন্য মুখোশ নৃত্য তিব্বত-বাংলার অন্যান্য প্রাচীন আদান-প্রদানের সাথে আদিবাসী সমাজে প্রবেশ করেছিল? যেখানে মানভূম গবেষক দিলীপ কুমার গোস্বামী শিবের গাজনে মুখে কালি মেখে বা মুহা বা মুখোশ পরে নাচকেই ছৌ নাচের আদি রূপ বলে মনে করেছেন। এইপ্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গের চৈত্র সংক্রান্তির উৎসবের সময়ের মালদা জেলার গম্ভীরা গানের সাথে মুখোশ নাচের প্রসঙ্গ চলে আসবে। গম্ভীরা নৃত্যের মুখোশ হিসাবে বিভিন্ন ধরনের মুখোশ বিশেষ করে, হিন্দু পৌরাণিক চরিত্রের বাণ, কালী, নরসিংহী, বাশুলী, গৃধিনীবিশাল, চামুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, ঝাঁটাকালী, মহিষমর্দিনী, লক্ষ্মী-সরস্বতী, হিরণ্যকশিপুবধ, তাড়কাবধ, শুম্ভনিশুম্ভ বধ ইত্যাদির মুখোশ ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় সূত্রধর সম্প্রদায় নিম এবং ডুমুর গাছের অংশবিশেষের সাহায্যে মুখোশগুলি তৈরি করে। কখনও কখনও মুখোশগুলি মাটি দিয়েও তৈরি করা হয়। এই মুখোশের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় নরসিংহী মুখোশ। বিশিষ্ট গবেষক ও অধ্যাপক পুষ্পজিৎ রায়ের উদ্যোগে তাঁর ছাত্রদলের সংগৃহীত এই মুখোশ ওনাদের সবুজ অবুঝ শিশু অঙ্গন স্কুলে পড়ার সময় কিম্বা ওনার বাড়িতে আমি অনেকবার দেখেছি। আপনারাও কোচবিহার রাজবাড়ির জাদুঘরে দেখে নিতে পারেন। এই মুখোশের সাথে তিব্বতী মুখোশগুলির ব্যাপক মিল আছে। মুর্শিদাবাদের আলকাপের মত গম্ভীরার শিব ও জনতা কিম্বা দাদু-নাতির কথোপকথন কিম্বা প্রশ্নোত্তরের সাথে জৈন পর্যুসন উৎসবে প্রশ্নোত্তর ও উপদেশ প্রদান প্রথার মিল আছে। মালদার আদিনা(ফারসি ভাষায় জুম্মা) মসজিদকের শিবে যে রূপের মন্দির বলে দাবি করা হচ্ছে, সেই আদিনাথ আসলে জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ। আদিনা মসজিদের গায়ে মুর্তিগুলো কিছু কিছু ছিল আগের বৌদ্ধ আর জৈন মন্দিরের পাথরের। এই জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরগুলো সেন রাজারা ধ্বংস করেন। যখন দাবি করা হয়, বৌদ্ধদেবী তারাকে হিন্দু বানানো হয়েছে, তখন শৈবধর্ম নামে পরিচিত হওয়া তিব্বতি লোকাচারের প্রভাবিত অংশটিতে জৈন আদিনাথের আত্তীকরণ হয়েছিল কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা উচিৎ। আদিনা মসজিদের আসেপাশেই ব্যাপক আকারে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস আছে। ১৯২০র দশকে কাশীশ্বর চক্রবর্তী মালদায় সর্বে সহায় নামে একটা সংগঠন তৈরি করেন। সাঁওতালদের ক্ষত্রিয় উপাধি দেওয়া হয়। জিতু সাঁওতাল আদিনা মসজিদের গায়ে কালী মুর্তি বসিয়ে দখল করতে গেলে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গণিখানের বাবা আবুল হায়াত খান লস্কর পাঠিয়ে দমন করেন। এখনো আদিনা মসজিদের গায়ে ওই ঘটনার গুলির দাগ রয়ে গেছে। সেসময় আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ জমিদারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল। পরবর্তীতে এই জমিদারদের বংশধর গণিখান চৌধুরী ও কৃষেন্দু চৌধুরী কংগ্রেস ঘরানার রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পেলে বাম আমলে জিতু সাঁওতালের হিন্দুত্বপন্থী ইতিহাস মুছে তাঁকে কৃষক নেতা বানানো হয়। এমনকি প্রায় আট দশক আগের হুল বিদ্রোহের সাথে মিলিয়ে সিধুকানুজিতু মেলা চালু করা হয়।
ঠিক এখান থেকেই আরেকটি প্রশ্নের জন্ম হয়। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে কুপল্যান্ডের ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার মানভূম গ্রন্থে ছৌ নাচের কোন উল্লেখ না থাকায় অনেকে মনে করেন ১৯১১-এর পরে ছৌ নাচের উদ্ভব হয়েছে, অন্তত মানভূম অঞ্চলে।
অন্যদিকে ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাতো ও ডঃ সুধীর করণের মতে এই নাচের নাম ছো, আবার বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত ও ডঃ বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতোর মতে এই নাচের নাম ছ। তার সাথে ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাতো, 'জঙ্গলমহল-রাঢ়ভূম ও ঝাড়িখণ্ডের ভূমিব্যবস্থা' বইটিতে জানিয়েছেন, "বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি ও লাফ ঝাঁপ দেওয়াকেই বলে ছো করা। আমার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি দেখে আমার মা আমাকে বকতেন- পড় বেটা পড়, কি ছো যে করছিস?" দিলীপ কুমার গোস্বামী, 'সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি' বইতে জানিয়েছেন অনাড়ম্বর মুখোশ সহকারে একক ছৌ বা 'এ কৈড়া ছো' নাচের উদ্ভব হয়। এ কৈড়া ছো নাচের পরে 'আলাপ ছো' বা 'মেল ছো' নাচের উদ্ভব হয়, যেখানে মুখোশ ছাড়া দুইজন বা চারজন নর্তক নাচ করতেন। এছাড়া সম্ভ্রান্ত বাড়ির নর্তকরা আড়ম্বরপূর্ণ সাজপোশাক পরে 'বাবু ছো' নামক একপ্রকার নাচের প্রচলন করেন। এই নাচে ধুয়া নামক ছোট ঝুমুর গান গাওয়া হয়ে থাকে। ১৯৩০-এর দশকে 'পালা ছো' নাচের সৃষ্টি হয়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম ছ বা ছো নাচের পরিবর্তে ছৌ নামে অভিহিত করেন এবং বিদেশে এই নাচের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার পরে এই নাচ ছৌ নাচ নামে জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। সুধীর কুমার করণ, 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' বইতে বলেছেন, "ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও ছৌ নামকরণের পক্ষে কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ দেখাতে পারেননি। এমনকি ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে শুধুমাত্র ছৌ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ছো নাচের দল নিয়ে বিদেশে যাবার সময় ছো-কে ছৌ-তে রূপান্তরিত করেই বিদেশে নিয়ে যান এবং এই সময় থেকেই ছৌ নামেই ডাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে কোলকাতার মঞ্চে-ও ছৌ নামেই তাঁর আগমণ ঘটে এবং সীমান্তবাংলার অধিবাসীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তা চলতেই থাকে।"
এখানে প্রশ্ন ওঠে এই নাচে শিবের গাজনের জায়গায় দুর্গাপুজোর উপকরণ যোগ করা, তাকে ছৌ নাম দেওয়া, কি কোন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অংশ? স্বাধীনতার পরে পরে বিভিন্ন লেখকদের লেখা থেকেই পাওয়া যায় খন্ডিত ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রভাষ্য কি হবে এই নিয়ে চিন্তা। সেসময় যেরকম জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়, তেমনই সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখাতে শিক্ষা-সংস্কৃতি-স্থাপত্যের নীতি বিষয়ক প্রবন্ধের পাশাপাশি ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনরায় আবির্ভাব নিয়ে আলোচনাও চোখে পড়ে। এই সময়তেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুঙ্গভদ্রার তীরে(১৯৫৮), কুমারসম্ভবের কবি(১৯৬১) বা বহু যুগের ওপার হতে(১৯৬৫) প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকাশ পায়। প্রায় এই সময়তেই শরদিন্দুর কলমে ফিরে আসেন ব্যোমকেশ বক্সী, যার নতুন কোন গল্প ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭এর ফজলুল হক, নাজিমুদ্দীন, সোহরাওয়ার্দীর শাসনকালে প্রকাশিত হয়নি। অনেকেই জেনে থাকবেন ১৯৫৫র 'পথের পাঁচালি'ও সরকারি অর্থানুকূল্যে প্রযোজিত হয়। ফলে খন্ডিত 'পশ্চিমবঙ্গে'র বিশেষ করে কলকাতাভিত্তিক কৃষ্টিভাষ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটা প্রয়াস তখন চলছিল এটা স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে। ছৌ নাচের এই বিবর্তনও কি এই প্রক্রিয়ারই অংশের অন্তর্গত? এটা প্রত্যক্ষ বা সচেতনভাবে হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের সমাজভাবনারচর্চাগুলোতে এইদিকটাকেও জিজ্ঞাসায় আনতে হবে।