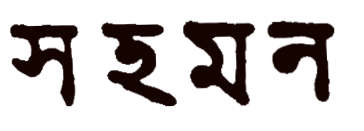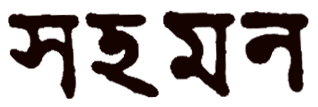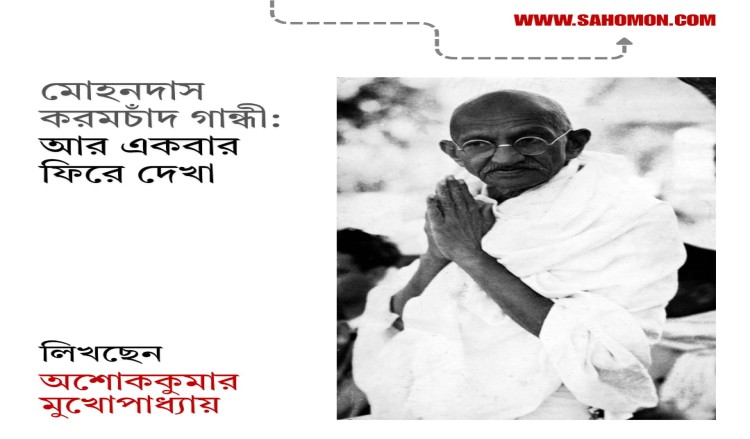ব্যক্তিগতভাবে একজন ঘোষিত মার্ক্সবাদী হিসাবে আমার মতবাদিক অবস্থান স্বভাবতই কট্টর গান্ধীবাদ বিরোধী — সেটা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর চর্চিত জীবন দর্শন এবং আচরিত কর্মপন্থা, সর্ব ক্ষেত্রেই। তবু আজ দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁকে স্মরণ করে দুচারটে প্রীতি ও অপ্রীতির কথা বলতে চাই। স্বীকার করতে বাধা নেই, একজন বস্তুবাদী ইতিহাস বীক্ষকের সাদা চোখেও কখনও কখনও পুরনো ভাবনার পুনর্মন্থনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে এটা খুব সংক্ষিপ্ত অবলোকন। এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বিচার বা মূল্যায়নের অবকাশ নেই। রূপদর্শী (গৌরকিশোর ঘোষ)-এর ভাষায় একে আমার কোনো এক ২ অক্টোবর তারিখের “সোচ্চার চিন্তা” হিসাবেই পেশ করতে চাই।
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সৌভাগ্যই বলতে হবে, হিন্দু ধর্ম নিয়ে আজীবন অনেক কুসংস্কার চর্চা, দৃশ্যত অনেক বাড়াবাড়ি করা সত্ত্বেও তিনি যে মনের গভীরে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী ছিলেন না, জঙ্গি হিন্দু মৌলবাদীদের অস্ত্রাঘাতে নৃশংস মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেটা প্রমাণ করার সুযোগ পেলেন। ভারতের প্রথম পঞ্জীকৃত (হিন্দু) জঙ্গি নাথুরাম গদসের বন্দুক মোহনদাসকে শুধুই মারেনি, তাঁর সম্মানকে বাঁচিয়েও দিয়েছে। হিন্দুরাষ্ট্রের ফেরিওয়ালাদের সামনে তিনি যে একজন প্রাচীরতুল্য বাধা স্বরূপ ব্যক্তিত্ব — এটা ওরা উত্তরকালের সকলের বোঝার জন্য মোটা হরফে ইতিহাসে লিখে দিয়ে গেছে।
ফ্যাসিস্ত দক্ষিণপন্থার তুলনায় দক্ষিণপন্থী গান্ধীকেও আজ খানিক সৎ উদারনৈতিক গণতন্ত্রপ্রেমী চরিত্র বলে চিহ্নিত করা যায়! মোশা-রাজ এইভাবেই গান্ধীকে আমাদের বামপন্থীদের কাছে এনে দিয়েছে।
এক
প্রথমেই লক্ষণীয়, গান্ধীর চিন্তায় ও আচরণে মধ্যে প্রচণ্ড স্ববিরোধ ছিল। ভালো মন্দের। ভুল ঠিকের। জাতিবাদ বনাম উদারতার। ধর্মীয় রক্ষণশীলতা আর প্রশস্ততার। নীতি গ্রহণ ও বর্জনের। জেদ ও শোধনের। না, এই স্ববিরোধিতা ঠিক স্বামী বিবেকানন্দের মতো নয়। একই কালে দুই দেশে দুরকম বক্তব্য নয়। শ্রোতা অনুযায়ী বক্তব্যের সুর পালটানো নয়। এ ছিল তাঁর চেতনায় এক ধরনের অনিবার্য দোলাচল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানসিক দৃঢ়তার দৃষ্টিকটু অভাব। অন্য বহু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব। শেষ বিচারে ইতিহাসে সমাজে অচেতনে শ্রেণিগত ভূমিকা পালনের বাধ্যতা বনাম সেই ভূমিকার অন্যায্যতায় সজ্ঞান মনোবেদনা। অমোঘ কায়েমি শ্রেণিস্বার্থের চাপ তাঁকে দিয়ে ভারতীয় উঠতি বানিয়াদের অর্থনৈতিক ও তদনুযায়ী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও রূপায়ণ করিয়ে নিতে চায়; আর তাঁর এক স্বতস্ফূর্ত জনদরদি মন এক রকমের অবাস্তব সদিচ্ছা নিয়ে তার বিপ্রতীপ মার্গে তাঁকে পদচারণা করতে আবেদন জানাতে থাকে — এই দ্বন্দ্বসংঘাতের নিরসনে তিনি এক বাস্তবিক অপারগতার শিকার। যিনি যত বড়ই হন, ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা তাঁর ইচ্ছা বা সদিচ্ছা দিয়ে নির্ধারিত হয় না, হয় তাঁর সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে সচেতন প্রয়াসের দ্বারা। মোহনদাস গান্ধীর জীবন ও চরিত্রকে সামনে রেখে আজ সেই শিক্ষাটা আরও একবার বাজিয়ে দেখা যেতে পারে। বিশেষ ঐতিহাসিক কালে কারও ভূমিকা সমকালীন সামাজিক চাহিদা অতিক্রম করতে চাইলেও যেমন বিপদ, তাকে ছুঁতে না পারলেও আবার এক রকমের উলটো বিপত্তি এসে দেখা দেবেই। ঘটনাচক্রে, গান্ধীর ক্ষেত্রে এই দুই বিপত্তিরই দেখা মেলে।
আসুন মিলিয়ে নিই এক এক করে।
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর যোগদান যথেষ্ট বিলম্বিত। জৈন এবং বানিয়া পরিবারের স্বাভাবিক পরম্পরা অনুযায়ী টাকা রোজগারের ধান্দায় (আলোচ্য ক্ষেত্রে বিকল্পহীন এই শব্দটা ব্যবহারের জন্য আমি আন্তরিক ভাবে ক্ষমা প্রার্থী) দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করে তিনি নিজেকে স্বেচ্ছায় এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ থেকে বহু কাল সরিয়ে রেখেছিলেন। দেশের পরাধীনতার জ্বালা তখন তাঁকে তেমন ভাবে পীড়িত করেনি, কোনো সংগ্রামের আহ্বান তাঁর অন্তরে সাড়া জাগাতে পারেনি। আমার কেবলই মনে হয়, জোহানেসবার্গ-এর সেই রেল স্টেশনে এক সাদা সাহেব তাঁকে কালা আফ্রিকান নেটিভ ভেবে রেল গাড়ির প্রথম শ্রেণির কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে না দিলে ভারতীয়দের হয়ত জাতি হিসাবে পিতৃহীন হয়েই থাকতে হত। এমনকি আজও। সেই সাহেবকে তাই মরণোত্তর শত শত ধন্যবাদ দিই আমি, না জেনে এই একটা ভালো কাজ করে ফেলার জন্য! গান্ধীকে তাঁর স্বদেশের আম আদমির অপমান যন্ত্রণা অনুভব করার প্রথম বারের মতো সুযোগ দিয়ে।
পাশাপাশি, যখন তিনি অবশেষে দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিলেন, ৪২ বছর বয়সে, তিনি এমন কয়েকটি কাজ করলেন, যার ঐতিহাসিক দীর্ঘমেয়াদি মূল্য অনেক। এই ক্ষেত্রে গান্ধীর অন্তত দুটো বড় অবদান আমাদের অবশ্য স্বীকার্য।
এক, তিনি এই আন্দোলনকে তিন দশক ব্যাপী ইংরেজি শিক্ষিতদের সীমাবদ্ধ প্রতিবাদী অভিভাষণ ও স্মারকলিপি নিবেদন থেকে বের করে এনে বৃহত্তর গণ আন্দোলনের আকার দিতে সক্ষম হন। সশস্ত্র বিপ্লবীদের একক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি সন্ত্রাসের মাধ্যমে শাসকের মনে ভয় ধরানোর বীরত্বপূর্ণ কিন্তু অকার্যকর পদ্ধতিরও বিকল্প হয়ে ওঠে তাঁর এই গণ বিক্ষোভ কর্মসূচি। তাঁর চরকা কর্মসূচি সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস যাই হোক, তা নিয়ে র্যাডিক্যাল মনন থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (“swaraj can be won by soldiers, not by spiders”) কিংবা কাজী নজরুল ইসলাম (“সূতা দিয়া মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুনি”)-দের স্বল্প প্রচারিত সমালোচনাকে যুক্তির আলোকে অগ্রাহ্য করা যায় না। স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে এটা একেবারেই কোনো বড় হাতিয়ার ছিল না। এমনকি, ইংরেজ শাসকদের জন্যও তা বিন্দুমাত্র কোনো ভয়ের কারণ ছিল না। তা হলেও, আম জনতার হাতে দেশের কাজ করার একটা রূপক কর্মসূচি হিসাবে চরকা একটা গণ চরিত্র অর্জন করে এবং তাদের মানসলোকে স্থায়ী আসন পায়। এ ছিল এমন একটা কর্মসূচি যেখানে ঘরের আবদ্ধ মহিলারাও আধ ঘন্টা চরকায় সুতো কেটে মনে মনে স্বদেশপ্রেমে যুক্ত হয়ে যেতে পারতেন।
তিনি অহিংসার নাম করে যে সমস্ত আন্দোলন পদ্ধতি নির্বাচন করেন — সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, অনশন, ধর্না, ইত্যাদি — অনেকের কাছেই সেগুলো গ্রহণযোগ্য সহজপাচ্য কর্মসূচি হয়ে ওঠে। সকলেই অক্লেশে সানন্দে যোগদান করতে পারে। সেই থেকে আজ অবধি আমরা বামপন্থীরাও গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেই একই ক্রিয়াপন্থা ব্যবহার করে চলেছি। ইউরোপ থেকে পাওয়া ধর্মঘটের বাইরে একটাও নতুন পদ্ধতি আমরা নিজেরা এখনও উদ্ভাবন করে বের করতে পারিনি। যদিও, সময় হয়েছে গণ আন্দোলনের নতুন পদ্ধতি অনুসন্ধানের।
দুই, তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত সার্বক্ষণিক সর্বস্বত্যাগী কংগ্রেস রাজনৈতিক সেবকদের জন্য আশ্রমের পরিকল্পনা করেছিলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপনও করেছিলেন বেশ কয়েকটি আশ্রম। সেই সব গান্ধী আশ্রম আজও নিবু নিবু হয়ে টিকে আছে। এমনকি বাংলাদেশেও একটি রয়ে গেছে। অথচ প্রায় একই সময়ে গড়ে ওঠা বামপন্থী দলগুলির প্রতিষ্ঠিত অনেক কমিউন পার্টিমেস ইত্যাদি আমাদের চোখের সামনেই একে একে লাটে উঠে গেছে।
এছাড়া, ব্যক্তিজীবনে তিনি কখনও ক্ষমতা ও সুবিধার জন্য লালায়িত ছিলেন না। কংগ্রেসে অসাংবিধানিক সীমাহীন কর্তৃত্ব পেয়েও তাকে তিনি পরিবারতন্ত্রে ব্যবহার করেননি শুধু নয়, ছেলেদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন তাঁর নাম ব্যবহার করে কখনও আখের গোছানোর চেষ্টা না করে। এখনকার দিনের কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল ইত্যাদি দলের নেতা মন্ত্রীদের দেখে দেখে এই কথাটা নিশ্চয়ই বেশি করে মনে পড়তে বাধ্য।
দুই
পক্ষান্তরে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধী তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষতি করেছেন তিন জায়গায়। যদিও সেটা তাঁর অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছায়।
এক, “অহিংসা”কে একটা কৌশল (policy) হিসাবে গ্রহণ করার বদলে একে তিনি একটা মৌল নীতি (creed) হিসাবে চালু করতে চান। অথচ, বাস্তবে তাঁর এই অহিংসা কোনো সার্বত্রিক ভাবে প্রযোজ্য নীতি ছিল না, ছিল কেবলমাত্র ব্রিটিশদের সাপেক্ষে অনুসৃত। অন্যদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের ব্যবহৃত হিংসাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন ও সক্রিয় ভাবে সাহায্য করেছেন। প্রায় আজীবন। বিনা দ্বিধায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থানীয় আদিবাসীদের বিরুদ্ধে, চিনের বিরুদ্ধে আফিম যুদ্ধে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও। টাকাপয়সা তুলে দিয়েছেন, মাল সরবরাহ করেছেন, সেনা নিয়োগে সহায়তা করেছেন। এমনকি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থানীয় জনজাতির বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক যুদ্ধে ইংরেজ শাসকরা প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্য থেকে সেনা নিয়োগে রাজি না হওয়ায় (হয়ত ভরসা না পাওয়ায়) তিনি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সংগঠিত করে সেই দস্যু দখলদারদের বেশ খুশি মনে অকুণ্ঠিত চিত্তে সাহায্য করেছেন। সেই হিংসার পক্ষে দাঁড়াতে তাঁর অহিংসা-বিবেকে এতটুকুও বাধেনি। তাঁর জীবনীকাররাও এই কাজকে অনায়াসে, বিবেকের সামান্য খোঁচাও অনুভব না করেই, তাঁর এক মহান কর্তব্যপরায়ণতা হিসাবে দেখিয়ে থাকেন। অথবা না দেখে নিঃশব্দে খাতার পাতা থেকে মুছে দেন। অথচ, সেই সব ক্ষেত্রে নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে হিংস্র শাসকের অস্ত্রের ব্যবহারে তাঁর অহিংসার পূজারী প্রাণ মন বিবেক যে কাঁদেনি, সেই সব কাজ যে তাঁর বহুপ্রচারিত অহিংসা নীতির সঙ্গে একেবারেই যায় না — তা নিয়ে তাঁকে কেউ কোনো দিন আক্ষেপ করতেও দেখেনি বা শোনেনি। জীবনের শেষ ভাগেও না।
এমনকি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুয়র যুদ্ধে ইংরেজদের প্রবল ভাবে নিন্দা করেছেন, তিনিও সেই যুদ্ধে গান্ধীর হিংসার পক্ষে অবস্থানকে যেন দেখেও দেখেননি। তার পরেও গান্ধীকে “মহাত্মা” সম্বোধনে তাঁর কলম কেঁপে ওঠেনি।
তার পরেও যে তিনি বিশ্বে আইনস্টাইনের মতো অনেকের কাছে অহিংসার পূজারী হিসাবে গণ্য ও বন্দিত হয়েছেন, সে নিতান্তই পরাধীন ও স্বাধীন ভারতের ক্ষমতাশীল ও ক্ষমতাসীনদের উদ্দেশ্যপূর্ণ নিরন্তর তথ্যবর্জিত ফাঁপা স্তুতিমূলক প্রচারের গুণে। রমাঁ রলাঁ অবশ্য এই প্রচারের ঢক্কানিনাদ এক সময় ধরে ফেলেছিলেন! কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই প্রচারের সুযোগে হিংসা অহিংসার প্রশ্নটা স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল লক্ষ্যের চাইতেও বড় হয়ে উঠেছে। মূল লক্ষ্যকে গৌণ করে ফেলা সম্ভব হয়েছে।
দুই, অহিংসাকে নৈতিক ও মানসিক শক্তি হিসাবে প্রচার করলেও রাজনীতিতে বিরোধীদের ক্ষেত্রে এই অহিংসার পূজারী বরাবরই দৃশ্যকটুভাবে বারংবার অত্যন্ত অনৈতিক অবস্থান নিয়েছেন। সে গোপীনাথ সাহার ঘটনায় হোক, যতীন দাস-এর আত্মাহুতি বা ভগৎ সিং-দের ফাঁসির ঘটনায় হোক, অথবা সুভাষ বসুর দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের সময় হোক। কিন্তু শুধু মাত্র অর্থ উপার্জনের সময়কার কোটপ্যান্ট ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে যোগী বেশ পরে থাকার দরুন ভারতীয় জনমানসে — এমনকি, অনেক শিক্ষিত মননেও — সেই সব অনৈতিক কার্যাবলি ইতিহাসে অনায়াসে চাপা পড়ে গেছে এবং চাপা দেওয়া গেছে।
এর একটা চিরস্থায়ী বিষময় ফল হয়েছে এই যে কংগ্রেসি তথা দেশের ঘরোয়া রাজনীতিতে দ্বিচারিতা ও অনৈতিকতা একটা প্রামাণ্য আচরণ বিধি হিসাবে বেশ মর্যাদা পেয়েছে।
তিন, পারিবারিক ভাবে জৈন হলেও এক রামাশ্রিত বৈষ্ণব ধর্মীয় ভাবাবেগ থেকে তিনি এক দিকে স্বাধীনতা আন্দোলনকে বৃহত্তর হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে প্রায় একাত্ম করে দিতে চেয়েছেন। এটা করতে গিয়ে তিনি হিন্দু ধর্মের সমস্ত আচার বিচার কুপ্রথাগুলিকে বিভিন্ন ভাবে সমর্থন যুগিয়েছেন, সম্মান বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন সময় অনেক অবৈজ্ঞানিক কথাও বলেছেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বললেও, হরিজন শব্দের আমদানি করলেও, ব্রাহ্মণ্যবাদ সৃষ্ট ও পুষ্ট জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কার্যকরীভাবে একটি কথাও বলেননি, বরং নানা কায়দায় তাকে যুক্তিসম্মত প্রমাণ ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা চালিয়েছেন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত হিন্দুত্ববাদীদের সবচাইতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্লোগান ও কার্যক্রম গোরক্ষা আন্দোলনের একজন নিরন্তর উচ্চবাক প্রবক্তা ছিলেন তিনি।
ফলে তিনি যখন মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর কর্মসূচিতে টেনে আনতে চান, সেও মুসলিম সমাজের অগ্রসর ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত অংশকে সঙ্গে নিয়ে নয়, তাদের মধ্যে পিছিয়ে পড়া চেতনাকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়েই। খলিফাতন্ত্র নামক এক মধ্যযুগীয় ধর্মাশ্রিত সামন্তরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে তিনি আধুনিক স্বাধীন ভারত গড়ার স্বপ্নের সাথে তালগোল পাকাতে গিয়েছেন সাম্প্রদায়িক ঐক্যের নামে। তাতে না পেরেছেন তিনি তাদের মেলাতে, না পেরেছেন তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে সামনের দিকে তাকাতে বলতে। রাম কাম খলিফা মিলে সাম্প্রদায়িক “সম্প্রীতি”র যে স্বপ্ন তিনি খাড়া করেন, তা যত দিন গেছে স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিভক্তই করেছে, ঐক্যবদ্ধ করেনি। মুসলিম লিগের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের সমান্তরালে তারই হাত কেটে বাড়তে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দু মহাসভা প্রচারিত দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রকরণ মেনে নিয়ে পাকিস্তানের দাবিতে পর্যবসিত হয়।
তিনি যে হিন্দু ধর্মের সুর ভাঁজতে থাকেন তা শেষ বিচারে ব্রাহ্মণ্যবাদেরই গুনগুনানি হয়ে উঠতে থাকে। তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ তাঁর প্রকল্পিত আসন্ন রামরাজত্বে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির যে নিশ্চিতি পান তাতে তাদের দুশ্চিন্তা জেগে ওঠে। তাই তারাও শেষ অবধি যে স্বতন্ত্র দলিত মুক্তির আন্দোলন গড়ে তোলেন তা স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ হিসাবে নয়, তার সমান্তরালে এক অন্য পক্ষ হয়ে ওঠে।
পক্ষান্তরে, আসল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যথার্থই অনুভব করে, গান্ধীর আন্দোলনে তাদের চাহিদা মতো সনাতন ব্রাহ্মণ্যবাদের স্পষ্ট ঘোষণা ও পক্ষপাতিত্ব নেই। সনাতন ধর্মকেই একমাত্র প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প নেই। এক উদার সর্ব ধর্মের সমন্বিত ভারতের স্বপ্নই তাতে দুর্বলভাবে হলেও বন্দিত। মুসলমান তাঁর শত্রু নয়। সুতরাং তারাও আর এক ভিন্ন ধারায় পূর্ণাঙ্গ ব্রাহ্মণ্যবাদের দাঁত নখ সহ নিজস্ব ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সঙ্ঘ পরিবারের আবির্ভাব ও কার্যক্রমও, এক দূরাগত অর্থে, গান্ধীবাদেরই অবশ্যম্ভাবী অনিচ্ছাকৃত প্রতিক্রিয়া জনিত পরিণতি।
গান্ধীর শক্তিশালী নেতৃত্বের আবেশেই স্বাধীনতা আন্দোলন এই ভাবে চতুর্ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। বা বলা ভালো, স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি মন্দক তিনটি ধারার জন্ম হয়।
তিন
আশ্চর্যের হলেও একটা কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁর জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে নিজের এই মহিমান্বিত ভুলগুলি — অন্যেরা ধরতে না পারলেও — অনেকটাই একে একে বুঝতে পেরেছিলেন। সে অনেকটাই আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীন সাফল্য ও বাহ্যিক ব্যর্থতার টুকরো টুকরো খবর থেকে। যে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের অনেক সাধনা করেও তিনি প্রায় কিছুই করে উঠতে পারলেন না, সুভাষ বসু সেটা তাঁর বাহিনীতে সফল করতে সক্ষম হলেন কী মন্ত্রে? ইতিহাস দেখল, সেই একই রক্ষণশীল গান্ধী তারপর রাজনীতি থেকে ধর্মকে ছেঁটে ফেলতে আগ্রহী হয়ে পড়েন। সেই গান্ধীই অহিংসার ঠুন্কো চুরিগুলি ফেলে দিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর আটক শস্ত্রধারী সেনাদের নানা ভাবে সাহায্য করতে ব্যস্ত হন। তাঁকে সক্রিয় হতে দেখেই নেহরুও হঠাৎই সুভাষ প্রেমিক হয়ে জনপ্রিয়তার ঘোলা পানিতে মাছ ধরতে আইএনএ-এর সেনানীদের পক্ষে মামলা লড়তে নেমে পড়েন।
আবার সেই গান্ধীই তখন চূড়ান্ত হিন্দু মৌলবাদী গোরক্ষার আওয়াজকে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সরিয়ে দিতে, সংবিধানের পাতায় ঢোকানোর বিরুদ্ধে কলম তুলে নেন। তখন তিনি যেন এক ভিন্ন চরিত্র। এক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা, সেদিনের হবু রাষ্ট্রপতি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন প্রায় সঙ্ঘ প্রচারকের মতো করে সংবিধান রচনা পরিষদে গোহত্যা নিবারণের ধারা সংযোজনের জন্য দেশ জোড়া প্রয়াসে নিমগ্ন, গান্ধী তাঁকে বারণ করছেন এই সব বাড়াবাড়ি করতে। তখন তিনি যুক্তি দিচ্ছেন যুক্তিবাদীদের মতো, সচেতন সমাজকর্মীর মতো করে। প্রশ্ন করছেন, দেশে গোহত্যা নিবারণ করে যে গরু তোমাদের দেশওয়ালি বানিয়া ভাইরা বিদেশে রপ্তানি করছে, তারা কি জানে না, সেখানে সেই গরুদের নিয়ে কী করা হবে? লক্ষ করুন, আজ বিজেপি নেতা সঙ্ঘ প্রচারক এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক গো-রপ্তানি বানিয়াদের উদ্দেশে আমাদেরও কিন্তু এই একই প্রশ্নবাণ।
ভারতের ইতিহাসের এবং জনগণের দুর্ভাগ্য, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। একমাত্র তখনই তিনি আবিষ্কার করলেন, তিনি ছাড়া পৃথিবীতে যথার্থ অর্থে আর কোনো গান্ধীবাদী নেই। ভারতীয় বুর্জোয়াদের ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনায় কিংবা নেহরু প্যাটেলদের গদি আদায়ের কৌশলে তাঁর প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে গেছে। তাঁর পদপ্রান্তে এযাবত ভিড় জমিয়ে বসে থাকা গান্ধীটুপি পরিহিত বানিয়ারা এবং কংগ্রেসি নেতারা তাঁকে তখন রাজনীতির গুদামে বা শো-কেসে পুরে ফেলতে চান। তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেন। দেশ ভাগের পরিকল্পনায় কীভাবে তাঁকে প্যাঁচে ফেলে রাজি করানো যায় তার অঙ্ক কষেন! এবং সফলও হন।
ভারতের বুর্জোয়াদের গান্ধী নির্ভর কাজ তখন প্রায় হাসিল হয়ে গেছে। জনরোষ জাগিয়ে তুলে ইংরেজ শাসকদের উপর চাপ সৃষ্টি করে গণবিপ্লবকে আপাতত ঠেকিয়ে দেওয়া গেছে। {এখন আমরা জানি, বেশ অনেক দিনের জন্য বুর্জোয়া শ্রেণি এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিভূরা সফল।} দেশের বাজার, প্রাকৃতিক সম্পদ আর শাসকীয় কুর্সি হাতের নাগালে এসেই গেছে। ফলে “রঘুপতি রাঘব . . .” গানের ধুনে গলা মেলাতে তারা আর তখন গান্ধীর পেছন পেছন হাত জোড় করে ঘোরে না।
গান্ধীকে তখন মর্ত্যধাম থেকে সরিয়ে দেওয়া নিতান্ত সহজ কাজ হয়ে যায়! নানা তরফে। হাতে হাতে হত্যা নাথুরাম গদসেই করে, কিন্তু এতদ্সংক্রান্ত আশঙ্কা ও কানাঘুসোয় শ্রুত গুজব সত্ত্বেও তাদের জন্য অনেকটা খোলা নিরাপদ খেলার জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়। এমনকি, নাথুরামকে যারা উদ্বুদ্ধ করে পাঠিয়েছিল, যে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল, তাদের যে সেই আসল চাঁই — ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক এবং একমাত্র মুচলেকা বীর — তাঁকে নানা রকম দূর নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় পুলিশি তদন্তের প্রক্রিয়া থেকে কায়দা করে বাইরে রেখে দেওয়া হয়। ফাইলের গতি শ্লথ করে রাখা হয়, যাতে গন্তব্যে পৌঁছতে অনির্দিষ্ট কাল দেরি হতে থাকে। অবশেষে সেই চাঁই মারা গেলে সেই তদন্তেও ইতি টানা হয়।
রঘুপতি রাঘব রাজারাম পতিত . . . — এইখানে এসে সেই ধুন থেমে গেছে! আজ আমরা অনুভব করি, তাঁর শেষ উচ্চারিত “হে রাম” তখন এক অদূর ভাবী কালের হা-রাম অভ্যুত্থানের তুর্যধ্বনি হয়ে ওঠে। রাম মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে রাম ভক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর বলিদান আবশ্যক হয়ে ওঠে। ২২ জানুয়ারি আবাহনের সঙ্গে ৩০ জানুয়ারির সংঘটন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।
আধুনিক কালের ইতিহাসের ছাত্ররা এবং সমাজ বদলের কর্মীরা যত তাড়াতাড়ি এই কথাগুলো ভেবে দেখবেন, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।