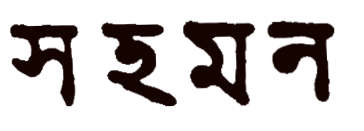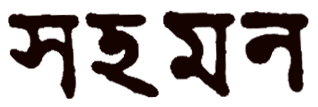গ্রামবাংলার রাজনীতি (প্রথম অংশ)
এইভাবে, গ্রামবাংলার রাজনৈতিক জীবনে সংগঠিত রাজনীতির প্রভাব যে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল সেই ১৯২০-৩০-এর দশক থেকেই, তার যথেষ্ট প্রমাণ কৃষক আন্দোলনের গবেষকদের লেখা থেকে পাওয়া যায়। ‘সংগঠিত রাজনীতি’ বলতে কি বোঝায়? ‘সাবলটার্ন স্টাডিজ’ এর গবেষকদের ধারণা অনুযায়ী,
আধুনিক রাষ্ট্র ক্ষমতা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার যে ক্ষেত্রটি উন্মুক্ত করে, তাতে সমস্ত জনসাধারণ অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারেন।... সমাজ কাঠামোর মধ্যে নবগঠিত রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের অনুপ্রবেশ এবং রাষ্ট্র-ক্ষমতার আইনি-রাজনৈতিক পরিসরে ক্ষমতা-সম্পর্কগুলির রূপান্তর একটা বিশেষ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ-পর্বে এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করতে হলে রাজনীতির ক্ষেত্রটাকে আমাদের দুটো ভাগে ভাগ করতে হবে। একটা রাষ্ট্রের বেঁধে দেওয়া আইনি-রাজনৈতিক নীতিমালা অনুযায়ী সংগঠিত, অপরটি এর বাইরে থাকা একটি ক্ষেত্র।
প্রথমটিকে যদি আমরা সংগঠিত রাজনীতির ক্ষেত্র বলি, দ্বিতীয়টি তাহলে অসংগঠিত রাজনীতির ক্ষেত্র। প্রথমটি যদি হয় রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক, দ্বিতীয়টিকে বলা যায় গণ-কেন্দ্রিক। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংগঠিত রাজনীতির চেহারাটা আমাদের খুবই পরিচিত। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক দল, শিক্ষিত সমাজ এবং প্রচারমাধ্যম এই সংগঠিত রাজনীতিকেই রাজনীতির মূল ধারা বলে জাহির করে। গণমানসে এমনভাবে এই রাজনীতিকে তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যাতে জনগণ এর বাইরে কিছু না ভাবেন, রাষ্ট্রের বেঁধে-দেওয়া আইনি রাজনীতির পরিধির মধ্যেই যাতে জনগণ সর্বদা আবদ্ধ থাকেন। এক কথায়, ‘জনগণ যেন আইনের শাসনকে মেনে নেয়’। জনগণের আন্দোলন উদ্যোগ বিদ্রোহ যেন আইনি কাঠামো বা তার বেঁধে দেওয়া সীমাকে ছাপিয়ে না যায়।
কিন্তু ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে, বিশেষ মুহূর্তে বা সন্ধিক্ষণে রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা না করে, অভিজাত শাসকদের বেঁধে-দেওয়া নীতি-নৈতিকতার সীমা উল্লঙ্ঘন করে নিম্নবর্গের জনগণ নিজেদের পৃথক সত্তা, পৃথক অস্তিত্ব, পৃথক চেতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। সেই বিশেষ সন্ধিক্ষণে জনগণই শেষ কথা বলে। নিম্নবর্গের মানুষ, যারা সমাজের প্রান্তে পড়ে থাকেন অন্য সময়, তারাই সশব্দে উঠে আসেন রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে, ইতিহাসের চালকের আসনটি কেড়ে নেন জোর করে। তখন তারাই প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসের স্রষ্টা হয়ে ওঠেন।
কিন্তু সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি ইতিহাসের রাশ কখনই নিম্নবর্গের মানুষর হাতে ছেড়ে দিতে চায় না। রাষ্ট্র চায় তার আইন-কানুন-সংবিধানের নিগড়ে বাঁধা থাকুক সকল গণউদ্যোগ। তার মধ্যে সে হাত-পা ছুঁডুক, তার মধ্যে সে বেড়ে উঠুক, কিন্তু কখনই সে যেন রাষ্ট্রের চেয়ে বড়ো হয়ে না ওঠে, রাষ্ট্রের সীমানাটা পেরিয়ে যেন মাথা না তোলে। রাষ্ট্রকে যেন ছাপিয়ে না যায়। ইতিহাসে সম্ভবত একবারই রাষ্ট্রের এক কর্ণধার জনগণের প্রতি আহ্বান রেখেছিলেন রাষ্ট্রকে ছাপিয়ে যেতে, রাষ্ট্রের ওপরে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে। মাও জে দং আহূত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সেই কর্মকাণ্ড শেষ পর্যন্ত ধিকৃত হয়েছে মাও-পরবর্তী চীনা রাষ্ট্র নায়কদের দ্বারা। গণ উদ্যোগের মুখে আরও শক্ত করে পড়ানো হয়েছে রাষ্ট্রীয় লাগাম। ‘বাড়াবাড়ি’ রুখতে আরও কড়া হয়েছে শাসনের চাবুক।
মাও জে দং-ই সম্ভবত প্রথম নেতা যিনি ‘হুনান কৃষক আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট’-এ জীবন্তভাবে দেখিয়েছেন যে, কৃষক আন্দোলন মানেই হলো বাড়াবাড়ি, ভদ্রলোক অভিজাতদের ভাষায় যা ‘ভয়ানক’ ব্যাপার-স্যাপার, ‘নিকৃষ্টদের আন্দোলন’ ইত্যাদি। মাও ওই রিপোর্টে এটাও দেখিয়েছেন যে, কৃষকদের নিজস্ব একটা চেতনা আছে। তারা অজ্ঞ নন, তাদের মধ্যেও জ্ঞান আছে। হুনান কৃষক আন্দোলন যে ‘১৪টি মহান সাফল্য’ অর্জন করেছিল, তার জন্য মাও কোথাও কমিউনিস্ট পার্টির পিঠ চাপড়াননি, বরং গোটাটাই কৃষকদের অর্জিত সাফল্য, তাদেরই চেতনার ফসল হিসাবে দেখিয়েছেন। এদেশের মাওবাদীরা আজ যখন তাদের বেশিরভাগ ক্রিয়াকর্মকেই পার্টির সাফল্য হিসাবে তুলে ধরতে প্রয়াসী হন, তখন সন্দেহ হয়, তারা কৃষকদের নিজস্ব চেতনা নিজস্ব উদ্যোগের ওপর আদৌ কতোটা নির্ভর করছেন। সকল ঘটনার নায়ক যদি পার্টি হয়, তাহলে বিপ্লবী আন্দোলনেও নিম্নবর্গের মানুষ ব্রাত্য হয়েই থেকে যান। প্রান্তদেশ থেকে উঠে এসে আন্দোলনের রঙ্গমঞ্চে কখনই তারা কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে পারেন না। জনগণ তথা নিম্নবর্গের মানুষ পার্টির কাছে লক্ষ্যবস্তু হয়েই থেকে যান, যাদের বিপ্লবী আন্দোলনে ‘টেনে আনতে হবে’, ‘সচেতন করতে হবে’, ‘পরিচালিত করতে হবে’, ‘সংগঠিত ও সমাবেশিত করতে হবে’ ইত্যাদি। এই গোটা কর্মকাণ্ডে পার্টিই কর্তা হয়ে থেকে যায়, জনগণ নয়।
কিন্তু যে কোনও সত্যিকারের গণবিদ্রোহ বা গণবিপ্লবে জনগণই কর্তার ভূমিকা নেন। জনগণের প্রান্তীয় যে অংশটা সমাজের বিকাশে নীরবে কাজ করে চলেন, যাদের ‘ঘামের তেলে ধনীর ঘরে আলো জ্বলে’, তাদের মধ্যেও থাকে এক অন্তর্লীন চেতনা, যা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়, দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতে শাণিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে ঝলসে ওঠে, তাকেই আমরা বলছি অসংগঠিত রাজনীতির ক্ষেত্র। আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও জনগণকে একটা ‘লক্ষ্যবস্তু’ হিসাবে দেখে, যার কাছে পৌঁছে দিতে হবে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সুফল, যাকে যুক্ত করতে হবে আর্থিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচীর সাথে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও নিদারুণ অনটনের সময় যার কাছে পৌঁছে দিতে হবে রিলিফ।
১৯২০-৩০ দশকের যে ইতিহাস আমরা আলোচনা করছিলাম, সেটা ছিল এদেশে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠার ঊষাকাল। সংসদীয় ব্যবস্থার বীজ তখন সবে বপন করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সীমিত। বিদেশি দখলদারী শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের চেতনা তখন ক্রমপ্রসারমান। ফলে, তখন রাষ্ট্রের সাথে জনগণের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ কমই ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রকে ঘিরে সচল হয়ে ওঠা সংগঠিত রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টির প্রভাব কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণির মানুষের মধ্যে খুব কম ছিল না। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক এই রাজনৈতিক দলগুলো যেমন কিছু পরিমানে রাষ্ট্র ও জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, তেমনি আবার রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজও করেছে। বিধান পরিষদে একটা মাত্রায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এছাড়াও গ্রাম-সমাজকে প্রভাবিত করেছে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই কিছু ধর্ম-ভিত্তিক দল বা শক্তি। কৃষক সংগ্রামের উন্মীলনে তারাও একটা ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে কৃষকরাও এই সমস্ত শক্তিকে অবলম্বন করে কোথাও ব্রিটিশ-বিরোধী, কোথাও-বা জমিদার-বিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।
এইভাবে সংগঠিত ও অসংগঠিত রাজনীতি একে অপরের সাথে সম্মিলিত হয়েছে, একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। এই দুই রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক, নির্ভরতা ও সংঘাত বাংলার গ্রাম-সমাজের ইতিহাসকে নির্ধারণ করেছে। গ্রাম-বাংলার সামাজিক ইতিহাসকে তাই এই দুই রাজনীতির আন্তঃসম্পর্কের ইতিহাস হিসেবে দেখা যায়, যেখানে উচ্চবর্গের সংগঠিত পার্টি-রাজনীতির প্রভাবে নিম্নবর্গের মানুষ সুদীর্ঘ সময় আচ্ছন্ন থেকেছেন, আবার বিশেষ সন্ধিক্ষণে নিম্নবর্গের মানুষ রাষ্ট্রীয় নীতিনৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করে স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অসংগঠিত রাজনীতির এই প্রকাশ সংগঠিত পার্টি-রাজনীতির ওপরে ছাপ ফেলেছে। রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণের যে ক্ষেত্রটি উচ্চবর্গের জন্য সদা-সংরক্ষিত, সেখানে নিম্নবর্গের অসন্তোষ-বিক্ষোভ-বিদ্রোহ একটা ‘বিষয়’ হয়ে উঠেছে, যা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রটিকে প্রভাবিত করেছে, পরিবর্তিত করেছে। কখনো-বা সংগঠিত রাজনীতির চলতি ছকটিকে উলটে দিয়েছে।
অর্থাৎ এদেশের শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস শ্রেণি-রাজনীতির কোনও সরল-রৈখিক ছকে-বাঁধা পথে এগোয়নি। চীন-বিপ্লবের ইতিহাসে বিপ্লবী রাজনীতির পেছনে সর্বহারা ও আধাসর্বহারা শ্রেণিগুলোকে যে পদ্ধতিতে ঐক্যবদ্ধ করা গিয়েছিল, এদেশে সেভাবে বিপ্লবী শ্রেণিগুলির ঐক্য গড়ে ওঠেনি। গড়ে তোলা সম্ভবও ছিল না। রাজনীতির শ্রেণিভিত্তি থাকলেও, শ্রেণিগুলি যে রাজনীতির ভিত্তিতেই বিভাজিত হবে, এমন কোনো কথা নেই। আধুনিক রাষ্ট্রের উন্মেষের সাথেসাথে সর্বহারা শ্রেণির মধ্যেও বুর্জোয়া রাজনীতি ভিত গাড়ে। তখন সেই রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করে সর্বহারাশ্রেণীকে বিপ্লবের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম মুখ্য হয়ে ওঠে। রুশ বিপ্লবের পথনির্দেশ কালে লেনিন একারণেই রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক সংগ্রামের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।
এদেশে সংগঠিত পার্টি-রাজনীতির অনুপ্রবেশের ফলে সেই ১৯২০-৩০-এর দশক থেকেই বাংলার গ্রামসমাজে রাজনীতির বিকাশ হয়েছে আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে। আমরা দেখেছি, কোথাও মুসলিম মৌলভিদের প্রেরণায় কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠেছে, কোথাও বা হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সংস্পর্শে কৃষক আন্দোলন উৎসারিত হয়েছে। আবার মেদিনীপুরে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছে। কৃষক জনসাধারণের মধ্যে সংগঠিত পার্টি-রাজনীতির এই প্রভাব-প্রতিপত্তিকে মোকাবিলা না করে বিপ্লবের অগ্রগতির কথা ভাবা বা বলা একেবারেই অবান্তর। এর সাথে যুক্ত ধর্ম ও বর্ণ তথা জাতপাতের প্রভাব। এই দুই-এর প্রভাব সংস্কৃতি ও মতাদর্শের স্তরে, জনমনের গভীরে। সংগঠিত পার্টি-রাজনীতি ধর্ম ও বর্ণ-বিভাজনের ওপর ভিত্তি করেই এদেশে তাদের জাল-বিস্তার করেছে।
তেভাগা-কালে গ্রাম-রাজনীতি
১৯৪৭-এর ঠিক আগে-পরে গ্রামবাংলায় সংগঠিত পার্টি-রাজনীতির অনুপ্রবেশ ও প্রভাব দুর্বার গতিতে বেড়ে চলে। এই পর্বে পশ্চিমবাংলার কৃষক জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যান্য সংগঠিত দলগুলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায় বামপন্থী বিভিন্ন দল, যার মধ্যে অগ্রগণ্য কমিউনিস্ট পার্টি (অবিভক্ত)। ১৯৪৬-৪৯ সময়কালব্যাপী তেভাগা আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বাংলায় প্রথম বড়ো আকারের কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলন নিম্নবর্গের স্বকীয় রাজনীতির আত্মপ্রকাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা এই আন্দোলন সম্পর্কে পার্টি ও কৃষকসভা নেতৃত্বের পরিকল্পনা ও ধ্যানধারণাকে বহুগুণ ছাপিয়ে যায়।
এই আন্দোলন সম্পর্কে কৃষকসভার দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে ছিল ‘অর্থনৈতিক’, কৃষকরা সেখানে অচিরেই আন্দোলনকে তাদের মুক্তি আন্দোলনে পরিণত করেন। বিনয়ভূষণ চৌধুরীর লেখায় এর স্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায়,
তেভাগার সংগ্রাম এভাবে হয়ে উঠল ক্ষমতার জন্য বৃহত্তর সংগ্রাম। তেভাগার দাবি জোতদাররা মেনে নেবে কিনা--প্রশ্নটা এতো সরল ছিল না। মূল প্রশ্নটা ছিল গ্রামের জোতদারদের সুরক্ষিত কর্তৃত্বের কাঠামোটা টিকে থাকবে কিনা। বিদ্রোহী বর্গাদারেরা ক্রমশই এই দিক থেকে তাদের সংগ্রামকে দেখতে শুরু করেছিল। ভাগচাষীদের ক্ষমতার এই প্রশ্নটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন উপাদান।
এই নতুন উপাদানটি যে কৃষক-চেতনারই ফসল তা-ও এই লেখায় স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছেঃ
সমসাময়িক দলিলপত্রে কৃষকদের মনোজগতে পরিবর্তন, এই লড়াই-এ আরও বড় ঝুঁকি নেওয়া সম্পর্কে তাদের চেতনাবৃদ্ধির বিষয়গুলি বিধৃত আছে। প্রথমদিকে বাইরে থেকে যারা এই আন্দোলন সরেজমিনে পরিদর্শনে এসেছিলেন তাদের সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বর্গাদারদের মধ্যে এই বিষয়ে ব্যাপক প্রত্যয়-দৃপ্ত অনুভূতি যে, জোতদারদের ওপর নির্ভরতার জোয়াল ভেঙে তারা বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, এবং ‘তাঁরা এখন পুরোপুরি স্বাধীন’। বর্গাদারদের কাজকর্মের মধ্যেও এই উল্লাসের অনুভূতি ফুটে উঠেছিল। বিদ্রোহী বর্গাদারদের সচেতনতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, নীতিগতভাবে স্থানীয় পুলিশবাহিনী জোতদারদের সমর্থনে ব্যাপক আকারে মাঠে নেমে পড়ার আগেই ব্রিটিশ রাজের স্থানীয় কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে বর্গাদারদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। কৃষক সংগঠনগুলি তখন থেকে দোষী জোতদারদের শাস্তি দেবার অধিকার চাইল।
এই পর্বের কৃষক আন্দোলনে লক্ষ করার বিষয় হলো, সংগঠিত রাজনীতি এখানে কমিউনিস্ট পার্টির হাত ধরে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছচ্ছে, কিন্তু তবু নিম্নবর্গের চেতনা, নিম্নবর্গের রাজনীতির সাথে তার একটা তফাৎ থেকেই যাচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে যেমন নিম্নবর্গের মধ্যে নতুন চেতনার জন্ম হচ্ছে, তেমনি নিম্নবর্গের চেতনা কিন্তু ওপর থেকে নির্ধারিত কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনের কর্মসূচীকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, তাকে প্রভাবিত করছে, পরিবর্তিত করছে। আন্দোলনের গতিবেগে পার্টি পেছনে পড়ে থেকেছে। দেখা যাচ্ছে, পার্টি জনগণের চেতনাকে আত্মস্থ করে উঠতে পারেনি। ফলে, আন্দোলনের চাহিদাও পূরণ করতে পারেনি।
অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিও নিম্নবর্গের রাজনীতির প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারছে না। কমিউনিস্ট পার্টির গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ও সংগঠনের জাল বিস্তারের পরেও নিম্নবর্গের জনগণের চিন্তা-চেতনা ও সক্রিয়তার ক্ষেত্রটা পৃথকই থেকে যাচ্ছে। সংগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি এবং অসংগঠিত নিম্নবর্গের রাজনীতি এখানে এক গভীর আন্তঃসম্পর্কে যুক্ত হচ্ছে, একে অপরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে, গঠন করছে। আবার একে অপরের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। উভয়ের মিলনে তেভাগার মতো এক মহৎ আন্দোলনের জন্ম হলেও স্বকীয়তায় দুই রাজনীতি কিন্তু আলাদাই রয়ে গেছে।
এই পর্বে গ্রামবাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির অনুপ্রবেশ সংগঠিত পার্টি-রাজনীতির শিকড় আরও গভীরে বিস্তৃত করল। এর কারণ দ্বিবিধ। প্রথম কারণ, মতাদর্শগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের অনেক কাছে পৌঁছোতে পারে, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করতে পারে, জনগণকে নতুন দিনের স্বপ্নে উদ্ভাসিত করতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, সংগঠনগতভাবেও কমিউনিস্ট পার্টি তার শাখা-প্রশাখা ও গণসংগঠনগুলোর মাধ্যমে জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে পারে, ব্যাপক মানুষকে গ্রামস্তরেই সংগঠিত করতে পারে, গ্রামস্তরে নেতৃত্বদায়ী কর্মী গড়ে তুলে পার্টির সাথে জনগণের সেতুবন্ধন সুদৃঢ় করতে পারে। ফলে, নিম্নবর্গের মানুষ মতাদর্শ ও সাংগঠনিক উভয় দিক থেকেই এই পার্টির সাথে অনেকটা একাত্মতা বোধ করতে পারেন। সংগঠিত রাজনীতির প্রভাব এক্ষেত্রে গভীরতা ও ব্যাপ্তি দুদিক থেকেই অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রভাবকে ছাপিয়ে যেতে পারে।
(চলবে)
Partha Chatterjee, Bengal 1920-1947, (preface XXXviii),
'নিম্নবর্গ' শব্দটি বাংলায় Subaltern-এর প্রতিশব্দ হিসাবে চালু করেন সাবল্টার্ন স্টাডিজ-এর অন্যতম প্রবক্তা রনজিত গুহ। ভারতীয় সমাজকে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গে বিভাজন মূলত ক্ষমতা বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে করা হয়। উচ্চবর্গ বলতে যারা 'প্রভুশক্তির অধিকারী'---বিদেশি ও দেশি, সরকারি বা বেসরকারি যেসকল শ্রেণি, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি নানানভাবে সমাজে প্রভুস্থানীয় বলে গণ্য হয় এবং প্রভুত্ব খাটায় তাদের উচ্চবর্গ, আর বাকি সকলে নিম্নবর্গের মানুষ---এই অর্থে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ বিভাজনকে ধরা হয়েছে।
দ্রষ্টব্য: 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।
বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, 'সংগঠিত রাজনীতি' ও কৃষক বিদ্রোহ, অনীক, মার্চ-এপ্রিল ১৯৯৭।
সূত্রঃ ঐ