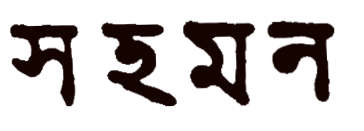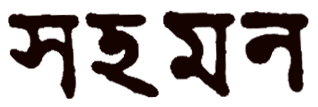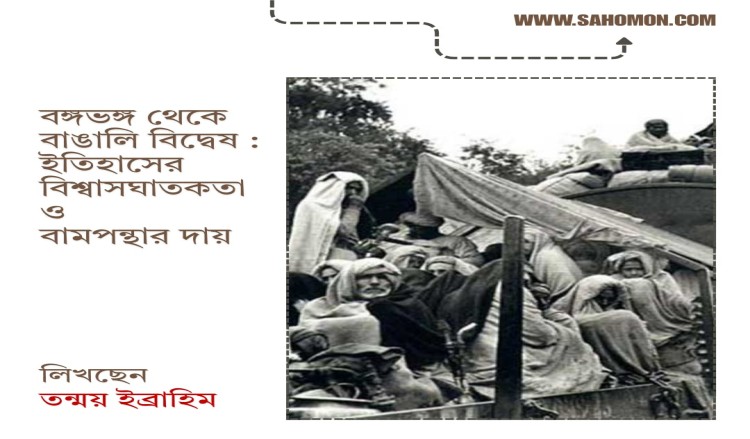সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
অনেক দশক পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বাঙালি পরিচয় একটি জ্বলন্ত ইস্যু হিসেবে উঠে এসেছে। বিগত কয়েক মাসে, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী শ্রমজীবী মানুষের উপর যে পুলিশি সন্ত্রাসের খাঁড়া নেমে এসেছে, তা শুধু রাজনৈতিক সংকট নয়, বরং এক গভীর ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতার ফসল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কাজের সন্ধানে যাওয়া বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের "বাংলাদেশি" তকমা লাগিয়ে আইনের তোয়াক্কা না করে সোজা বাংলাদেশে পুশব্যাক করার ঘটনা আসলে ১৯৪৭ সালের বঙ্গভঙ্গের দীর্ঘ ছায়া।
এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিক অক্সিজেন পেলেও, বাম শক্তির সামনে হিন্দুত্ববাদী ও হিন্দি আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কী দেখছি? ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) র রাজ্য কমিটির নেতা মহম্মদ সেলিম এই সংকটকে নিছক "বিজেপি ও তৃণমূলের নাটক" বলে খারিজ করে দিচ্ছেন। এই মন্তব্য শুধু রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা নয়, বরং বামপন্থার ঐতিহাসিক দেউলিয়াপনার প্রতিফলন।
ভারতীয় বামপন্থার মৌলিক সংকট
ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হলো বিদেশি মত ও পথের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং দেশীয় ইতিহাস ও বাস্তবতা সম্পর্কে উদাসীনতা। বামপন্থী ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীরা ভারতের শাসকশ্রেণীকে "৫,০০০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস" রচনা করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো: ভারত স্বাধীন হওয়ার ২০০ বছর আগে কি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী বা বেলুচিস্তান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত উপমহাদেশের মানুষ নিজেদের "ভারতীয়" বলে পরিচয় দিতেন?
এই কৃত্রিম "ভারতীয় সভ্যতা" তত্ত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে বামেরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) হিন্দু সভ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয় গঠনের প্রকল্পকে তাত্ত্বিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তারা নিজেরাই সেই একই "সভ্যতা" তত্ত্বের বাহক।
কলকাতার সাবর্ণ ভদ্রলোক ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান
দেড়শো বছরের ব্রিটিশ রাজধানী কলকাতায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। প্রথমত, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের রাজধানী হওয়ায় নিজেদের করণিকের যোগানের স্বার্থে ব্রিটিশেরা কোম্পানির আমল থেকেই কলকাতা শহরে পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারে উদ্যোগী হয়। যার ফলে, ব্রিটিশদের অধীনে চাকরি করে স্থায়ী উপার্জন করতে ও ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকার তাগিদ থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিরা কলকাতায় কেন্দ্রীভূত হন।
দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে, ব্রিটিশ শাসনের স্বার্থেই হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা ভাঙার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর ফলে বঙ্গীয় রেনেসাঁ জন্ম নেয়, যা মূলত কলকাতার সাবর্ণ হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সাবর্ণ সমাজই উনিশ শতকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। এরাই ‘ভারত’ দর্শনের প্রবক্তা হয়। এরাই চরম ইসলাম বিদ্বেষ থেকে চালিত হয়ে ব্রিটিশ শাসকদের কাছাকাছি থেকে সমস্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভাগিদারী চাইলো। প্রথমে নতজানু হয়ে, তারপর কংগ্রেসের মতন প্ল্যাটফর্ম বানিয়ে আর শেষ পর্যন্ত হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে। এই সম্প্রদায়ই কিন্তু উত্তর আর পশ্চিম ভারতে হিন্দুত্বের জিগির ওঠার অনেক আগেই "আনন্দমঠ" লিখে হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে এক আদিম সভ্যতার জয়গান শুরু করে। এই সম্প্রদায়ই কিন্তু ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল। বঙ্গ ভঙ্গ করার ব্রিটিশ অভিপ্রায় নিয়ে এরাই প্রশ্ন তোলে, জানতে চায় হিন্দু পশ্চিমের সাথে মুসলিম পূর্বের বিচ্ছেদ ঘটানোই কি এই বিভাজনের আসল কারণ? ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদে কাজ না হওয়ায়, বঙ্গ ভঙ্গ আটকাতে তারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। কিন্তু সেটা কি সত্যিই স্বাধীনতার জন্যে? কোন দেশের স্বাধীনতার জন্যে? বঙ্গের না পঞ্জাবের?
১৯০৫ সালের আন্দোলনে সাবর্ণ ভদ্রলোকদের যোগদানের মূলে ছিল পূর্ববঙ্গে তাদের জমিদারি হাতছাড়া হওয়ার ভয়। এই জমিদারিগুলো পূর্ব বাংলায় হলেও, জমিদারেরা অধিকাংশই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে থাকতেন। আর এই জমিদারি রক্ষার তাগিদ থেকে যে ভদ্রলোকেরা একদিন বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে ধরলেন, ৪২ বছর পরেই তারা কিন্তু বঙ্গ ভঙ্গ নিয়ে টু শব্দটিও করেনি।
বামপন্থী আন্দোলনে সাবর্ণ আধিপত্য
অনুশীলন ও যুগান্তর দলের ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত প্রায় সকলেই ছিলেন সাবর্ণ হিন্দু। মুসলিম তো দূরের কথা, দলিত বা নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও কখনো অংশ নিতে দেখা যায়নি। যদিও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আশরাফ মুসলিমেরা, অর্থাৎ উচ্চ জাতির মুসলিমরা, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার পরে বাংলার মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে নেতৃত্বে আধিপত্য বিস্তার করে সাবর্ণ হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা। কাকাবাবুর মতন দুই একজন টিম টিম করে জ্বলতে থাকেন। এই কারণেই সাবর্ণ হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা, জাতি-শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা সংগ্রাম গড়তে ব্যর্থ হয়। আর ব্যর্থ হয় বঙ্গীয় জাতির মানুষদের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে। ব্যর্থ হয় কারণ সে সর্বভারতীয় স্বার্থ কে বঙ্গের স্বার্থের জায়গায় অগ্রাধিকার দেয়।
সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতিকে গত শতকের চারের দশক থেকে রুখতেও তারা ব্যর্থ হয়। বাংলার মধ্যেই যে কমিউনিস্ট পার্টি তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারে তেভাগা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, সেই কমিউনিস্ট পার্টির চোখের সামনেই তেভাগা আন্দোলনে ব্যাপক কৃষকদের জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই কে আত্মসাৎ করে মুসলিম লীগ। বাংলার কমিউনিস্ট সংগঠকেরা যেখানে গ্রামে গ্রামে হিন্দু-মুসলিম কৃষকের শ্রেণী ঐক্য গড়ে তোলে জমিদারদের বিরুদ্ধে, মুসলিম লীগ সেই আন্দোলনে নেপোয় মারে দই করে — আপামর পূর্ব বাংলার মুসলিম কৃষকের লড়াইকে সে হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই বলে চালিয়ে দেয়। সেদিন কমিউনিস্ট নেতারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। তাঁরা হতভম্ব হয়ে দেখেন পাকিস্তান আন্দোলন কে। বাংলার কমিউনিস্ট নেতারা সেদিন বাংলা ভাগের চক্রান্ত কে দেখেও চুপ থাকেন।
বঙ্গভঙ্গ ও বামপন্থার বিশ্বাসঘাতকতা
বর্তমান বিজেপির প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী যখন বাংলা ভাগের পক্ষে, হিন্দু বাঙালি হোমল্যান্ড বানানোর দাবি নিয়ে হৈচৈ শুরু করেন, হিন্দু মহাসভার খুবই স্বল্প সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে, কমিউনিস্ট পার্টির ভদ্রলোক নেতৃত্ব কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে না। তাঁরা সেই সময়ে, যখন বাংলার অধিকাংশ দলিত, আদিবাসী, শূদ্র-নমঃশুদ্র মানুষ এবং মুসলিমের লেখা পড়া জানতেন না, নিজেদের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রাজনীতিকে আবদ্ধ রাখেন দিস্তা দিস্তা কাগজ ছাপানো ও মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে, যা সাধারণ হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে অবিশ্বাস কে ভাঙার কাজ করতে ব্যর্থ হয়।
কংগ্রেস, লীগ আর মহাসভা যখন বিভেদের রাজনীতি করছে, হিন্দু সাবর্ণ জমিদারদের একটা অংশ আর মাড়োয়ারি পুঁজিপতিরা যখন মুখার্জীকে চাঁদা দিচ্ছে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ কে ইন্ডিয়ার অধীনে রাখার, তখন কমিউনিস্ট পার্টির কাছে ছিল এক সুবর্ণ সুযোগ। তাঁরা লেনিনীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নে স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ বাংলার সমর্থনে দাঁড়াতে পারতেন, কিন্তু সেটা তাঁরা করেননি।
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুভাষ চন্দ্র বসুর অনুজ শরৎ চন্দ্র বসু, হুসেইন সোহরাওয়ার্দী ও কিরণ শঙ্কর রায় সেই বিভেদের দিনে, ১৯৪৬ সালের হানাহানির পরেও, এক সাথে বসে তৈরি করলেন স্বাধীন বাংলার রূপরেখা। যে বাংলার নাম তাঁরা দিলেন ঐক্যবদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক বাংলা। যে বাংলায় কৃষকের-শ্রমিকের অধিকারের কথা তাঁরা বললেন, সেই বাংলার প্রস্তাব কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও মেনে নিয়েছিলেন। যখন তিনি বুঝেছিলেন যে পাকিস্তান বানানো মানে একই দেশে দুই ব্যবস্থা চালানো কোনো মতেই সম্ভব না আর পূর্ব পাকিস্তান গড়লে তাতে শিল্পোন্নত কলকাতা ও তার পার্শবর্তী অঞ্চলকে কংগ্রেস বা মাড়োয়ারি পুঁজি কোনো ভাবেই হাত ছাড়া করবে না, তখন জিন্নাহ বলেছিলেন যে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলা হলে তিনি খুশি হবেন এবং সেই বাংলা পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকবে বলেও তিনি জানান। কিন্তু এই প্রস্তাবে কংগ্রেসের ভিতরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সেই আলোড়ন সৃষ্টি হয় কারণ মাড়োয়ারি আর হিন্দু জমিদারদের প্রতিনিধি মুখার্জীর মহাসভা এই বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে। মুখার্জী বড়লাট কে লেখেন যে ভারত ভাগ হোক বা না হোক, বাংলা ভাগ চাই। এই সময়ে দাঁড়িয়ে, বাংলার শ্রমিক কৃষকের ঐক্যের স্বার্থে, মাড়োয়ারি আর হিন্দি পুঁজির থেকে বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যের মুক্তির প্রশ্নে কমিউনিস্টদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ ছিল ঐক্যবদ্ধ বাংলার স্বার্থে লড়াই গড়ে তোলার, লীগকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার ও কংগ্রেসের দেশপ্রেমী অংশ কে নিজের দিকে টেনে নেওয়ার।কিন্তু সেই কাজ না করে কমিউনিস্টরা পাকিস্তান তৈরির পিছনে তত্ত্বের জাল বোনা শুরু করেন। দিস্তা দিস্তা লেখা ছাপান আর সেগুলো নিজেরাই পড়েন, সেগুলো নিয়ে নিজেরাই আলোচনা করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সাবর্ণ ভদ্রলোক নেতৃত্বের কাছে সেদিন অসুবিধার ব্যাপার ছিল যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশে তাঁদের পক্ষে থাকা ও রাজনীতি করা সম্ভব হবে না। তাঁরা সেই “ভারতীয় দর্শনের” তাড়নায় সেদিনও বাংলার জায়গায় ভারতকে রাখলেন। ১৯৪৭ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় তথাকথিত ভদ্রলোক-চালিত বামপন্থী শক্তি এক লহমায় তেভাগা আন্দোলনকে শিকেয় তুলে হিন্দুত্বের, হিন্দি আধিপত্যের পতাকা তুলে ধরে।
অনেকের না জানা থাকলেও, ১৯৬৪ সালে সিপিআই ভেঙে সিপিআই (এম) তৈরির আগেই, ১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত সিপিআই-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে, যেখানে বিটি রণদিভে তাঁর পূর্বসূরি পিসি যোশী সহ পুরো কেন্দ্রীয় কমিটির ভুল লাইনের সমালোচনা করেন, পার্টির প্রথম বড় ভাগ হয় — ভারত ও পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে। এই পার্টি ভাগ কিন্তু সেইদিন বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তে সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পাঞ্জাবি, মারাঠি, প্রভৃতি নেতৃত্বের সিলমোহর লাগানোর কাজ করে। এই দ্বিতীয় কংগ্রেসে একদিকে যেমন রণদিভের “ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়” স্লোগান ঘিরে হঠকারী লাইন গৃহীত হয়, তেমনি সেই ঝুটা স্বাধীনতার সাচ্চা বাংলা ভাগের পক্ষে সর্ব-ভারতীয় নেতৃত্ব তাত্ত্বিক যুক্তি হাজির করে।
যেখানে বামেদের উচিত ছিল বসু-সোহরাওয়ার্দীদের দাবি কে নিজের আওতায় এনে আরও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার, কৃষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই কে তীব্র করে মুখার্জীর লবি কে হারানো, সেই জায়গায় তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন উদ্বাস্তু আন্দোলন করতে। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি হওয়া মানুষদের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ভিত্তিতে বসবাসের কলোনি গড়ে তোলার লড়াইয়ে তাঁরা যোগ দেন। এ যেন মুখার্জীর হিন্দুত্ব আন্দোলনের সাপ্লিমেন্টারি একটি শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার একটি প্রয়াস ছিল বাংলার ভদ্রলোক কমিউনিস্ট নেতাদের।
হিন্দি আগ্রাসনের মুখে নিশ্চুপ কমিউনিস্টরা
ভারত আর পাকিস্তান সৃষ্টি করার পরে দুই দেশের শাসকের কাছেই জরুরী হয়ে ওঠে ভাষার প্রশ্নটি। হিন্দুস্তানী ভাষার থেকে সৃষ্ট উর্দু আর হিন্দিকে তারা আরও বেশি করে ধর্মীয় ভাবে ঘষে মেজে নিতে থাকে। এরই ফল স্বরূপ ভাষা আন্দোলন তীব্র হয় পূর্ব পাকিস্তানে। অন্যদিকে ভারতে হিন্দি কে রাষ্ট্র ভাষা করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পরে দ্রাবিড় জনগণ, বিশেষ করে তামিল নাড়ুর জনগণ। অসংখ্য মানুষের রক্তের বিনিময়ে আটকানো হয় কংগ্রেসের হিন্দি চাপানোর ষড়যন্ত্র। এই লড়াইয়েও বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃত্ব কে দেখতে পাওয়া যায়নি।
যদিও ভারত সরকার হিন্দি চাপানোর সিদ্ধান্ত কে গত শতকের ছয়ের দশকে স্থগিত করে, সংবিধানের হিসাবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ধীরে ধীরে ইংরাজি কে অবলুপ্ত করে হিন্দি কে চাপাতে বাধ্য, যদি না সংবিধান সংশোধন হয়। হিন্দি বা উর্দুর মতন কৃত্রিম ভাষাগুলো যে শুধুই ভাষাগত হামলা করে তাই নয় বরং সাংষ্কৃতিক হামলাও চালায়, ক্ষুদ্র ভাষা গোষ্ঠীগুলোকে, জাতিগুলোকে সাংস্কৃতিক ভাবে উপনিবেশে পরিণত করে, সেই ব্যাপারেও কমিউনিস্ট পার্টি কোথাও জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলেনি। ভদ্রলোক শ্রেণীও আসামের বরাক উপত্যকায় অহমীয় চাপানোর বিরোধিতা করে গুলি খায় কিন্তু কোথাও, পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলিমেরা যে ভাবে উর্দুর বিরুদ্ধে লড়ে গুলি খেয়ে প্রাণ দিলেন, সেভাবে হিন্দির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগিয়ে থাকেননি। বরং হিন্দি সাম্রাজ্যের তিনটি থাবাকে—সেনা বাহিনী, বলিউড ও ক্রিকেট দলের প্রতি সে আনুগত্য দেখিয়েছে এবং এদের মধ্যে ঢোকার আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু এই ভদ্রলোক বামেদের মুখে ঝামা ঘষে দেয় তাদেরই স্বজাতির এক কমিউনিস্ট নেতা।
বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ
১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা সিপিআই (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি যে সব জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার, স্বীকার করে। সিপিআই (এম-এল) প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি যার কর্মসূচী হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার, হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। আর এর মূল কান্ডারি হন বাংলার কৃষক নেতা চারু মজুমদার। তাঁর তিন বছরের নেতৃত্বে চারু মজুমদার শুধু সিপিআই (এম-এল) কে ভারতের শাসক শ্রেণীর এন্টিডোট হিসাবেই গড়ে তোলেননি, এই দলটিকে তিনি ভারতের শোষিত জাতির মানুষের কাছেও একটি বন্ধু হিসাবে উপস্থাপন করেন। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট বিপ্লবীরাও এর ফলে সাহস পান। কিন্তু চারু মজুমদার পরবর্তী সময়ে নানা রাজ্যে বেড়ে ওঠার স্বার্থে, বিশেষ করে হিন্দি বেল্টে সংগঠন বাড়ানোর তাগিদে, সিপিআই(এম-এল) দলের বিভিন্ন গোষ্ঠী হিন্দির বিরুদ্ধে অবস্থান থেকে সরে আসে ধীরে ধীরে।
বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও বামপন্থার ভূমিকা
যখন তৎকালীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট শক্তি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে, তখন দিল্লি প্রমাদ গোনে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাড়ির আন্দোলন আর পাশে পূর্ব বাংলায় একই আন্দোলন হলে অচিরেই দুটো মিলে যেতে পারে ভেবে শুধু দিল্লী না, মস্কোও প্রমাদ গোনে। ইন্দিরা গান্ধী আর মস্কোর লিওনিদ ব্রেজনেভ তাদের দুটো গুটিকে কাজে লাগায় বাংলার পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে। একদিকে মস্কোর অনুগত কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহ এবং অন্যদিকে অতীতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারী শেখ মুজিবুর রহমান। যে মুক্তিযুদ্ধ কমিউনিস্টরা শুরু করলো, সেটার নেতৃত্বে বসানো হলো মুজিব কে। মার্কিন অর্থে চলা পাকিস্তানী বাহিনীর বাঙালি অংশ যোগ দিল আওয়ামী সাথে। মস্কোর হুকুমে সিংহ নিজের দলের কর্মকান্ড সীমিত করে ফেলেন আওয়ামীকে সাহায্য করার মধ্যে।
তথাকথিত "মুক্তিযুদ্ধ" চলাকালীন কমিউনিস্টদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়নি মস্কো আর দিল্লির হুকুমে। কমিউনিস্টরা আওয়ামীদের হয়ে প্রচার করেছে, মেডিক্যাল ক্যাম্প করেছে আর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড করেছে, কিন্তু যুদ্ধ করেনি। বাংলাদেশ গঠনের সাথেই সিংহ যে শেখের সাথে ঐক্য করে মস্কোর হুকুমে নিজের দল কে আওয়ামী লীগে বিলীন করে বাকশাল গঠন করেন ও যে ভাবে কমিউনিস্ট পার্টি শেখের সমস্ত অপকর্মের সময় তার জোটসঙ্গী হিসাবে নীরব থাকে তার ফল দলটিকে আজও বাংলাদেশে ভুগতে হচ্ছে। একটি বৃহৎ সংগ্রামী দল থেকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আজ শুধুই বিবৃতি প্রকাশ করার পার্টিতে পরিণত হয়েছে। এই ১৯৭১ সালে যখন চারু মজুমদার ও সিপিআই(এম-এল) কংগ্রেসি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সহ নানা জায়গায় লড়ছে, তখনই কিন্তু কংগ্রেসীদের সাথে হাত মিলিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ভদ্রলোক নেতৃত্ব শ্রীমতি গান্ধীকে এশিয়ার মুক্তি সূর্য আখ্যা দেন।
বর্তমান সংকট ও ভদ্রলোক বামপন্থার দায়
আজ ৮০ বছর ধরে ভারতের বামেরা শাসকদের "৫,০০০ বছরের" ভারত সভ্যতার ইতিহাসের ওকালতি করে, নিজেদের দলগুলোকে দিল্লির দলে পরিণত করে সেই দিল্লির আধিপত্যের পক্ষে সাফাই গাইছে।কলকাতার খেতে-পরতে পারা ভদ্রলোকের সন্তানদের মধ্যেই বাম মনোভাব বেশি দেখা যায়, আর তারা বঙ্গীয় আত্মপরিচয় নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে। বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদ ভাবলেই তারা শিউরে ওঠে পারিবারিকভাবে লালিত-পালিত ইসলাম বিদ্বেষের কারণে। তারা মনে করে হিন্দি ভারতের রাষ্ট্র ভাষা। তাই মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় থেকে সেলিম সাহেব, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মতন তাঁরাও যে কোনো সময় হঠাৎ হিন্দি সংলাপ বলে আসর গরম করার চেষ্টা করেন। তাঁরাও বলিউড, ক্রিকেট আর সেনাবাহিনীর সম্মিলিত প্রয়াসে তৈরি ভারত দর্শনে বিশ্বাসী।
অথচ তারা জানে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসাম পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার ততদিন থাকবে যতদিন বাঙালি মুসলিম থাকবে। কারণ শেষ পর্যন্ত রাস্তায় নেমে বিজেপির সাথে লড়াই করার কাজ এই সম্প্রদায়ই করবে। এই সম্প্রদায়কেই নিজেকে বাঁচানোর জন্যে বাংলা ভাষা ও নিজের অস্তিত্ব কে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু তবুও তারা বাংলার আপামর দলিত, আদিবাসী ও মুসলিমদের থেকে নিজেকে বাঁচিয়েই রাখবে।
বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা
বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদকে বাদ দিয়ে আজ বাঙালির কথা বলা ধৃষ্টতা। আবার বঙ্গের নানা শোষিত জাতি—গোর্খা, কামতাপুরি, রাভা, সাঁওতাল, চাকমাদের কথা বাদ দিয়ে শুধু বাঙালি জাতীয়তার কথা বলাও উচ্চবিত্তের বিলাসিতার জাতীয়তাবাদ।
আজ নানা রাজ্যে বাঙালির উপর হওয়া উৎপীড়নের বীজ লুকানো আছে এই মাটির তলায়। সেই বীজ একা মুখার্জী রোপন করেননি। তাতে কমিউনিস্ট নেতাদেরও দায় আছে। যদিও সিপিআই(এম-এল) একবার চেষ্টা করেছিল, তবুও ব্যাপক ভাবে ভারতে আগ্রাসী হিন্দির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারাও বর্তমানে রাজনৈতিক বাধ্যকতার কারণে পিছিয়ে গেছে।বাঙালি নিপীড়ণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বাঙালি ভদ্রলোক সম্প্রদায় বিশ্বাসের অযোগ্য তাদের ইসলাম বিদ্বেষের কারণে। বাংলার কমিউনিস্টরাও ভরসার অযোগ্য তাদের দিল্লী প্রীতির কারণে। তবুও বঙ্গীয় জাতির মুসলিমরা ধর্মীয় মৌলবাদ ও দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগিয়ে থাকবেন। তাঁরা উর্দুর বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, হিন্দির বিরুদ্ধেও দেবেন। ভদ্রলোক সম্প্রদায় দেবে না।
এই পরিস্থিতে দাঁড়িয়ে মেকি বাম-হিন্দুত্ব চক্রান্ত ব্যর্থ করা একটি গুরু দায়িত্ব। বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সাম্য আন্দোলন গড়ে তোলাও আজ জরুরী। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন ইতিহাসের এই বিশ্বাসঘাতকতার মুখোমুখি হওয়া এবং সত্যিকারের গণমুখী রাজনীতি গড়ে তোলা।